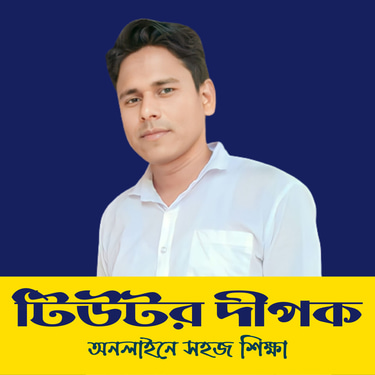প্রথম অধ্যায় [ইতিহাসের ধারণা]
■ বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর:
১. অ্যানালস গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-
(ক) সামাজিক ইতিহাস, (খ) খেলার ইতিহাস, (গ) শিল্পচর্চার ইতিহাস, (ঘ) পরিবেশের ইতিহাস।
২. সর্বপ্রথম নাট্যচর্চার উদ্ভব ঘটে-
(ক) চীনে (খ) গ্রীসে (গ) রোমে (ঘ) ভারতে।
৩. আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়-
(ক) ২৮ শে ফেব্রুয়ারি (খ) ৮ ই মার্চ (গ) ১৩ই এপ্রিল (ঘ) ১৩ই মে।
৪. ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র হলো-
(ক) বিল্বমঙ্গল (খ) রাজা হরিশচন্দ্র (গ) আলম আরা (ঘ) দেনা পাওনা।
৫. জীবনের ঝরাপাতা প্রকাশিত হয়- (ক) বঙ্গদর্শন (খ) ভারতী (গ) দেশ (ঘ) প্রবাসী পত্রিকায়।
৬. সোমপ্রকাশ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন-
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৭. ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা অবস্থিত-
(ক) কলকাতা (খ) মুম্বাই (গ) দিল্লি (ঘ) চেন্নাই-তে।
৮. হিস্ট্রি ফ্রম বিলোউ গ্রন্থটি রচনা করেন-
(ক) এ.পি. থমসন (খ) ইউজিন জেনোভিস (গ) হারবার্ট গুডম্যান (ঘ) রয় লাঁদুরি।
৯. বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট প্রতিষ্ঠা করেন-
(ক) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) নন্দলাল বসু।
১০. ভারতের নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা প্রথম শুরু করেন-
(ক) ডি.ডি. কোশাম্বি (খ) রজনীপাম দত্ত (গ) রনজিত গুহ (ঘ) পার্থ চ্যাটার্জী।
■ ঠিক/ভুল নির্নয় করো:
১. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ভারতের একটি গথিক স্থাপত্য শৈলীর উদাহরণ। (ঠিক)
২. ইন্দিরাকে লেখা জওহরলাল নেহেরুর লেখা চিঠিগুলির সংকলিত গ্রন্থ দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। (ভুল)
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর নাম হল জীবনস্মৃতি। (ঠিক)
৪. কে. টি. আচয় খেলাধুলার ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন। (ভুল)
৫. সোমপ্রকাশ পত্রিকাটির প্রকাশনা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার বন্ধ করে দেয়। (ঠিক)
■ এককথায় উত্তর দাও-
১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. ভারতের খেলার ইতিহাস চর্চা প্রথম কবে শুরু হয়?
উত্তর: ভারতের খেলার ইতিহাস চর্চা প্রথম শুরু হয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে।
৩. ভারতের কোন শহরকে সংস্কৃতির শহর বলা হয়?
উত্তর: কলকাতা শহরকে সংস্কৃতির শহর বলা হয়।
৪. মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে।
৫. ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক কে?
উত্তর: ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হলেন দাদাসাহেব ফালকে।
■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:
১. সামরিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব কী?
◆ সামরিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব:
কোন রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষা ও ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যখন ইতিহাস লেখা হয়, তখন সেই ইতিহাসকে সামরিক ইতিহাস বলা হয়।
সামরিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব হল-
(i) সামরিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে অতীত থেকে বর্তমানে যুদ্ধের প্রকৌশলগত পরিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়।
(ii) শাসকের সামরিক দক্ষতা ও গৃহীত রণকৌশল দ্বারা যুদ্ধ জয়ের ইতিবৃত্ত জানা যায়।
২. আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা কী?
◆ আত্মজীবনী:
সমাজের প্রতিষ্ঠীত কোনও ব্যক্তি যখন নিজের জীবন ও জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনাগুলোর বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাকে আত্মজীবনী বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জীবনস্মৃতি হল আত্মজীবনীর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
স্মৃতিকথা:
স্বনামধন্য ব্যক্তি যখন জীবনের একটা নির্দিষ্ট প্রান্তে উপনীত হয়ে তার পূর্ববর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি গুলিকে লিখিতভাবে গ্রন্থে রূপ দেন তখন তাকে স্মৃতিকথা বলা হয়। যেমন, বিপিনচন্দ্র পাল-এর লেখা সত্তর বৎসর।
৩. আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান রূপে সরকারি নথিপত্রের সীমাবদ্ধতা কী?
◆ সরকারি নথিপত্র বলতে পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা সংগৃহীত নথিকেই বোঝায়। এর সীমাবদ্ধতা গুলি হল-
(i) ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা সরকারি নথি সংগৃহীত হওয়ার দরুন তা ছিল অধিকাংশই পক্ষপাত দুষ্ট। কারণ, গৃহীত তথ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অন্ধ সমর্থন প্রকাশ পেত।
(ii) সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে তথ্যকে বিকৃত করে লেখা হয়।
(iii) সাধারণ মানুষের চাহিদা, অনুভূতি, ক্ষোভ-বিক্ষোভকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি।
৪. আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব কী?
◆ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলের ইতিহাসই হল আঞ্চলিক ইতিহাস। এই ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব হল-
(i) আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা জাতীয় ইতিহাসকে পরিপূর্ণতা রূপদান করে।
(ii) নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের ভাবনা ও তার ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হয়।
৫. পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্ব কী?
প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা-পর্যালোচনার ইতিহাসই হল পরিবেশের ইতিহাস। এই ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব গুলি হল-
(i) মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর পরিবেশের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
(ii) পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি ও পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।
৬. স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীকে কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান রুপে ব্যবহার করা যায়?
◆ আধুনিক ইতিহাস চর্চার উপাদান রূপে আত্মজীবনীয ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব:
(i) আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ থেকে লেখকের জীবন ও জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিবরণ পাওয়া যায়।
(ii) আলোচ্য বিষয় থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসেবে লেখক সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন, যা আধুনিক ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করে।
৭. সামাজিক ইতিহাস কী?
◆ সমাজ গঠনের মূল উপাদান হলো মানুষ। সেই মানুষের জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিক গুলি যেমন- খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে যে ইতিহাস রচনা করা হয় তা-ই হল সামাজিক ইতিহাস।
অতীতে সামাজিক ইতিহাস রচনায় রাজা-অভিজাতদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও ১৯৬০-৭০ এর দশক থেকে সাধারণ মানুষকে নিয়ে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার বিষয়টি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
৮. শহরের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
◆ আধুনিক ইতিহাস চর্চার যে ধারায় শহরের উৎপত্তি, বিকাশ, পতনের পাশাপাশি শহরের মানুষের জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে শহরের ইতিহাস বলা হয়। এই শহরের ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে-
(i) কোন একটি নির্দিষ্ট শহরের উত্থান, বিকাশ ও পতনের কাহিনী জানা যায়।
(ii) শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।
-এজন্য শহরের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।
৯. অ্যানাল স্কুল কী?
◆ ফ্রান্সের দুই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লুসিয়েন ফেভর ও মার্ক ব্লখ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যানালস অব ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ইতিহাস লেখার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করতে থাকে। পরবর্তীতে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তা অ্যানাল স্কুল নামে পরিচিত।
ফার্নান্দ ব্রদেল, রয় লাঁদুরি ছিলেন এই প্রত্রিকাগোষ্ঠীর অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অ্যানাল স্কুল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরাই সর্বপ্রথম নতুন সামাজিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।
১০. সোমপ্রকাশ পত্রিকাটির প্রকাশনা সাময়িক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন?
◆ দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ চলাকালীন কাবুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের কঠোর সমালোচনা করলে সোমপ্রকাশ পত্রিকাটি ব্রিটিশ বিরোধিতার অপরাধে লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের রোষানলে পড়ে। এইসময় সম্পাদক দ্বারকানাথ সরকারি অনুশাসন মেনে মুচলেকা জমা দিলেও ধার্য এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে অস্বীকৃত হন।
এই কারণেই সোমপ্রকাশ পত্রিকাটির প্রকাশনা সাময়িক কালের (১৮৭৮-৮০ খ্রিস্টাব্দ) জন্য বন্ধ হয়ে যায়।
■ ৪ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর
১. আধুনিক ইতিহাসচর্চায় খেলার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
■ খেলার ইতিহাসচর্চার গুরুত্বঃ
● সূচনা: খেলাধুলা আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিনোদনের পাশাপাশি শরীরচর্চা ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণেই খেলার ইতিহাসচর্চা সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।
◆ খেলার ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব সমূহ :
ক) খেলাধুলার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান: আধুনিক ইতিহাস চর্চায় খেলাধুলার ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় খেলার উৎপত্তিস্থল তার ধারাবাহিক বিবর্তনের কাহিনী। খেলার ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি,পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মানাকালা খেলার উৎপত্তিস্থল হলো পঃ আফ্রিকা।
খ) জাতীয়তাবোধের সঞ্চার: খেলাকে কেন্দ্র করে অতীত ও বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মোহনবাগান ক্লাব, ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে খালি পায়ে ফুটবল খেলে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে আই.এফ.এ.শিল্ড কেড়ে নিয়েছিল যা জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে কেবল মূর্ত প্রতীক নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় এই বিজয় ছিল দেশ বিজয়ের মত।
গ) বর্ণবৈষম্য রোধ: ১৯৩৬ খ্রি : বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণাঙ্গ দৌড়বিদ জেসি ওয়েন্স চারটি স্বর্ণপদক জয় করে হিটলারের জাত্যাভিমান চূর্ণ করেন। এই ভাবেই বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও খেলার ইতিহাসের এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে।
ঘ) নারী স্বাধীনতা: খেলায় নারীদের অংশগ্রহণ দেখে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও স্বাধীনতা বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। বিভিন্ন যুগে নারীদের মানসিক,সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরে খেলার ইতিহাসচর্চা।
ঙ) পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি:- জাতীয়তাবাদ, সমাজ বিবর্তন, সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি বিষয়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করে চলেছে খেলাধুলা। খেলাধূলার মাধ্যমে দুটি দেশ তাদের পুরোনো ঝগড়া-বিবাদ ভুলে ক্রীড়াঙ্গনে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
চ) খেলাধুলা কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চা:- সাম্প্রতিককালে খেলার গুরুত্ব অনুসন্ধানকল্পে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সমস্ত জায়গায় খেলাধুলার ইতিহাস চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জে. এ. ম্যাসন, রিচার্ড হোল্ড বা বোরিয়া মজুমদার, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ এর লেখা গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।
মূল্যায়ন : খেলাধূলার প্রয়োজন বিবিধ। শুধু বিনোদন বা অবসরযাপন নয়, সমাজের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে খেলাধুলার। খেলাধূলার ইতিহাসও আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের জীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রোমান কবি জুভেনাল বলেছেন, "মানুষ দুটো জিনিসের জন্য আকুল হতে পারে - রুটি ও খেলাধুলো।"
২. আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে বঙ্গদর্শন পত্রিকার গুরুত্ব আলোচনা করো।
■ আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান স্বরূপ বঙ্গদর্শন পত্রিকার গুরুত্ব:
● ভুমিকাঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সমসাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আলোচ্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তথ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক উপাদান। এই পত্রিকা থেকে সমকালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।
● রচনা ও প্রকাশ:- সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায়, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।
● গুরুত্ব সমূহঃ
ক) সমকালীন তথ্য: বঙ্গদর্শন পত্রিকা হতে সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি রাজনীত, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। এই পত্রিকা তত্কালীন ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তের হদিস দেয়।
খ) স্বদেশিকতার প্রসার: বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনি দ্বারা বঙ্গদর্শন পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাঙালি মননে স্বজাত্যবোধ গ্রথিত হয়। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি প্রথম প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীকালে বাঙালি তথা ভারতীয় বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।
গ) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার: বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'সাম্য' সহ বিভিন্ন প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাঙালি সমাজে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উন্মেষ ও প্রসার ঘটে।
ঘ) কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার কারণে কৃষক-স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কৃষকদের স্বপক্ষে ধারাবাহিক ভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে থাকে।
ঘ) সাহিত্যগোষ্ঠীর জন্ম: বঙ্গদর্শন কে কেন্দ্র করে সেসময় বাংলায় এক নতুন সাহিত্য গোষ্ঠীর জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাগুলি অসংখ্য সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার সঙ্গে বাঙালির ভাবধারার মেলবন্ধন ঘটাত।
● উপসংহারঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি ছিল সমকালীন যুগের একটি অতি জনপ্রিয় পত্রিকা। এটি বাঙালি জাতির মনে নতুন উদ্দীপনা, উৎসাহ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঞ্চার করেছিল। যা নতুন সমাজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৭০-এর এর দশককে বাংলার বঙ্গদর্শনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।
৩. আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসাবে সোমপ্রকাশ পত্রিকার গুরুত্ব আলোচনা করো।
■ আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় সোমপ্ৰকাশ পত্রিকার গুরুত্ব:
আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সমসাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানে সমৃদ্ধ এই পত্রিকা থেকে সমকালের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
ক) সমকালীন তথ্যঃ আলোচ্য পত্রিকা থেকে সমকালীন সমাজ,অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কার কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণ- এর কদর্য রূপ চিত্রায়িত করে ভারতীয়দের সম্মুখে।
খ) কৃষক স্বরূপ বর্ণনা: সোমপ্রকাশ পত্রিকা-ই প্রথম জনসম্মুখে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে। নীলকর সাহেবদের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়মিত স্থান পেত এই পত্রিকায়।
গ) সমাজ চেতনার উন্মেষঃ সোমপ্রকাশ পত্রিকা সমকালীন বাঙালি সমাজের সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা যেমন বাল্যবিবাহ,বহুবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশ ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করত। তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহের প্রসারেও সোমপ্রকাশ জনমত গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিল।
গ) রাজনৈতিক সমালোচনাঃ শিক্ষিত বাঙালি জাতি ১৮৫৮-র পূর্বে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সেভাবে সচেতন ছিল না। সোমপ্রকাশ- ই প্রথম বাংলায় রাজনৈতিক আলোচনার সূচনা করে।
ঘ) ব্রিটিশ বিরোধীতাঃ এই পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনের কথা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করত। দেশীয় স্বার্থবিরোধী ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল' সহ ব্রিটিশ সরকারের উগ্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশ করত এই পত্রিকা।
ঙ) সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাঃ জাতীয় রাজনীতি ও স্বাজাত্যবোধ এবং সামাজিক ঘটনাবলির পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান,সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও নিয়মিত বৌদ্ধিক চর্চা স্থান পেত সোমপ্রকাশ পত্রিকায়।
● উপসংহারঃ সোমপ্রকাশ ছিল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত একটি নিৰ্ভীক সাপ্তাহিক পত্রিকা। এতে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করা হতো। যার দরুণ পত্রিকাটি সরকারের আইনের কোপে পড়ে এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি পুনরায় প্রকাশিত হলেও পূর্বের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে কমে যায় এবং ধীরে ধীরে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।
৪. সরলা দেবী চৌধুরানী আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক হয়েছে?
■ আধুনিক ইতিহাস চর্চায় সরলা দেবী চৌধুরানীর 'জীবনের ঝরাপাতা'-র ভূমিকা:
● সূচনা: আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব অপরিসীম। সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের ঝরাপাতা' হল এমনই একটি গ্রন্থ। জীবনের ঝরাপাতা কাহিনীটি দেশ পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
জীবনের ঝরাপাতা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল-
ক) ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলঃ এই গ্রন্থ থেকে ঠাকুর বাড়ির শিশুদের জীবনচর্চা, দুধমা-ধাইমা দিয়ে সন্তান পালন, গৃহশিক্ষক প্রথা, নারী শিক্ষা, জন্মদিন পালন ইত্যাদির কথা জানা যায়।
খ) স্বাদেশিকতার বার্তা: বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরলা দেবী চৌধুরানী স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রচার করার জন্য লক্ষীর ভান্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্ত্রী মহামন্ডল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
গ) অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসঃ বাংলার নীল চাষী, বাগানের কুলি ও মজুরদের ওপর ব্রিটিশদের অত্যাচার ও অবিচারের কথা সরলাদেবী তাঁর এই গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখেন।
জানা যায়, ভারতী পত্রিকায় তিনি বিলিতি ঘুষি বনাম দেশি কিল নামে একটি প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছিলেন।
ঘ) রাজনৈতিক কার্যকলাপঃ সরলাদেবী বাঙ্গালী যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের অস্ত্র শিক্ষা প্রদানের জন্য গড়ে তোলেন প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি।
ঙ) ব্যক্তিগত জীবনঃ আলোচ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সরলাদেবী স্বামী বিবেকানন্দ-এর স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সরলাদেবী ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।
চ) সংস্কারমূলক তথ্য: জীবনের ঝরাপাতা থেকে সমকালীন সমাজে নারী শিক্ষা, নারী সমাজের বিভিন্ন আদব-কায়দা ও ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপের কথা জানা যায়।
● উপসংহারঃ 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে সরলাদেবী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অপরিহার্য দলিল। তাই আধুনিক ইতিহাসচর্চায় এই গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।
৫. আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরকারি নথিপত্রের ভূমিকা আলোচনা করো ।
■ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ সরকারি নথিপত্রের ভূমিকাঃ
● সূচনা: যেকোনো দেশের ইতিহাস রচনায় সরকারি নথিপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। সরকারি নথিপত্রগুলি সাধারণত State Archives বা National Archives-এ সংরক্ষিত থাকে। ইতিহাসের উপাদান রূপে সরকারি নথিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সরকারি দলিল- দস্তাবেজ, সরকারি নির্দেশনামা, গ্রন্থাবলি, চিঠিপত্র, আঁকা ছবি, পুলিশি রিপোর্ট, গোয়েন্দা রিপোর্ট, সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদন ইত্যাদি।
ক) সরকারি কর্মচারীদের চিঠি : সরকারি নথিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পদাধিকারী যেমন- পুলিশ, গোয়েন্দা বা সরকারি আধিকারিকদের রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের বিবরণ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি। এগুলি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা আধুনিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
খ) সরকারি প্রতিবেদন : সরকারি আধিকারিকরা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবেদন পাঠাতেন সরকারের কাছে। আন্দোলন বা গুপ্তবিপ্লবী কার্যকলাপ বা নিছকই দিনলিপি, এই সব প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় সরকারের গৃহীত নীতি ও উদ্দেশ্যগুলির কথা। মেকলে মিনিট(১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ) বা উডের নির্দেশনামা (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) এরকমই প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত।
গ) বিশেষ কমিশনের প্রতিবেদন: সরকার বিশেষ বিশেষ সমস্যার জন্য কমিশন গঠন করে এবং সেই কমিশন সরকারকে রিপোর্ট দিত। এই রিপোর্টে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। হান্টার কমিশন(১৮৮২ খ্রীঃ), সাইমন কমিশন(১৯২৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি প্রতিবেদনগুলি থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যায় তাই, এই প্রতিবেদনগুলি গুরুত্বপূর্ণ।
ঘ) চিঠিপত্রের আদান-প্রদান : সরকারি ব্যবস্থায় চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ঔপনিবেশিক আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তাদের চিঠিপত্রের ব্যাপক আদান-প্রদান ঘটত। এই চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনায় বিভিন্ন প্রস্তাবের যেমন আলোচনা করতেন, তেমনি কোন শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টাও করতেন। উল্লেখ্য, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা লর্ড কার্জনের চিঠি থেকে জানা যায়।
● উপসংহারঃ সরকারি নথিপত্র থেকে ইতিহাস রচনা করতে গেলেও ও গবেষকদের সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ- পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারি আধিকারিকদের রিপোর্টগুলি সরকারকে তোষামোদ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভুল ও বিকৃত করা হয়ে থাকে। তবে এইসব তথ্যকে অন্য তথ্যের সঙ্গে যাচাই করে ইতিহাস রচনা করলে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।
৬. বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী 'সত্তর বছর' বছর কিভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠেছে তা বিশ্লেষন
কর।
■ ইতিহাসের উপাদান রূপে 'সত্তর বছর'-এর গুরুত্বঃ
● ভূমিকা : আধুনিক ইতিহাস রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্মৃতিকথা বা আত্মকথন। প্রখ্যাত চরমপন্থী বিপ্লবী, বাগ্মী সমাজসংস্কারক ও লেখক বিপিনচন্দ্র পালের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হল 'সত্তর বৎসর। ১৯২৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত সত্তর বৎসর গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র তাঁর জীবনের প্রথম ২২ বছরের সমকালের বিবিধ ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন, যা আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ দলিল।
ক) লেখকের নিজস্ব জীবন বৃত্তান্ত : আলোচ্য গ্রন্থে বিপিনচন্দ্রের জন্মস্থান শ্রীহট্টের কথা, তাঁর পরিবার ও সমাজের কথা, কলকাতায় আসা, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবন ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়।
খ) সমকালীন বাংলার ইতিহাস : সত্তর বৎসর গ্রন্থটি সমকালীন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী। কেন-না বিপিনচন্দ্র উনবিংশ ও বিংশ দুটি শতাব্দীর পটপরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে সমকালীন ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সভা-সমিতির কার্যকলাপ, ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'ভারত সভা'-র প্রতিবাদ এবং নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা'-র জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ তথ্য মেলে।
গ) বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণালাভ : সত্তর বৎসর' থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতি যেমন- দোল, দুর্গোৎসব, যাত্রা-গান, পুরাণপাঠ ও বিবাহ প্রথার পাশাপাশি কলকাতার তৎকালীন সংস্কৃতি, মিশনারিদের প্রভাব, খাদ্যাভ্যাস ও বিধিনিষেধ (উল্লেখ্য, মদ্যপান ও মদ্যপান নিবারণী সমিতি)-এর কথা জানা যায়।
ঘ) নারীদের অবস্থার উল্লেখঃ তৎকালীন সমাজে নারীরা কীভাবে শোষিত হতো তার বর্ণনা এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়ানো যায়, সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র তাঁর এই আত্মজীবনীতে।
ঙ) ব্রাহ্মসমাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান : বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা কীভাবে নতুন সামাজিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন! ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দরা সমকালীন শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শের সঞ্চার করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ কার্যাবলীর কথা ও তার ভাঙ্গন সম্পর্কে জানা যায়।
● উপসংহার : আলোচ্য গ্রন্থটি অসমাপ্ত হলেও বিপিনচন্দ্র তাঁর এই আত্মজীবনীতে নিখুঁতভাবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'বাংলার সমাজ, কলকাতার অবস্থা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৭. আধুনিক ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি' কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে?
■ আধুনিক ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'-র গুরুত্বঃ
● সূচনা : আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলা কৃতী ও বিদগ্ধ মানুষের আত্মজীবনী। এই ধরনের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলা কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি', যেখানে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।
● প্রকাশঃ লেখকের আত্মকথনটি প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
● পরিসরঃ আলোচ্য আত্মজীবনীতে ১৮৬১ - ৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা ও স্বদেশকথা বর্ণিত হয়েছে।
● ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল : আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সূত্র ধরে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, রুচি, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক ও বিধি-নিষেধ, শিশুদের জীবনধারা, বালক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীত চর্চা এবং বয়ঃপ্রাপ্তির বর্ণনা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
● স্বাদেশিকতা : আত্মজীবনীর স্বল্প পরিসরে স্বাদেশিকতা নিয়ে অত্যন্ত সরস ভাষায় লেখক যে অনবদ্য আলোচনা করেছেন, ইতিহাসের যেকোনা ছাত্রকে তা মুগ্ধ করবে। সেই যুগে অভিজাত বাঙালি পরিবারে বিভিন্ন বিদেশি প্রথার প্রচলন শুরু হলেও স্বদেশের প্রতি অনুরাগও জাগ্রত ছিল। স্বয়ং কবির পরিভাষায়—"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশি প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান হিরদীপ্তিতে জাগিতেছিল"।
● রাজনৈতিক ঘটনাবলীঃ জীবনস্মৃতি'-তে রবি ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বাদেশিকতার বিভিন্ন সভায় ঠাকুরবাড়ির বালকদের যাগেদান, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ধুতি ও পাজামার সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় পরিচ্ছদ প্রচলনের চেষ্টা, স্বদেশি দেশলাই কারখানা বা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় যুবকদের উদ্যোগ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।
● হিন্দুমেলার প্রসঙ্গ : আত্মকথনে কবি নবগাপোল মিত্রের নেতৃত্বে 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যকলাপের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই হিন্দুমেলাই তৎকালীন ভারতবর্ষে স্বদেশভাবনার অন্যতম কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।
● মন্তব্য : অসম্পূর্ণতা ও স্বল্প পরিসর দোষে দুষ্ট হলেও রবিঠাকুরের আত্মজীবনী শুধু তার জীবনদর্পণ নয়, তা একাধারে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চলমান প্রতিচ্ছবি। সহজ-সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর এই কথন আধুনিক ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক।
৮. 'লেটার ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার' ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
■ ইতিহাসের উপাদান রূপে 'লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার':
● সূচনা: আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জওহরলাল নেহরুর 'লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার'। সমগ্র চিঠিগুলো প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস সম্বলিত বিষয় নিয়ে লেখা যা পুরোদস্তুর শিক্ষামুলক।
● চিঠির প্রেক্ষাপট : ১৯২৮-১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যখন নেহেরুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে শুরু হতে চলেছে এক বিশাল আন্দোলন, সেই সময় তিনি এলাহাবাদের পৈতৃক বাড়ি থেকে মুসৌরিতে থাকা ১০ বছরের স্নেহের কন্যা ইন্দিরা (গান্ধী)-কে মোট ৩০ খানি চিঠি লিখেছিলেন। জওহরলালের ইংরেজিতে লেখা চিঠি গুলি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের ল জার্নাল প্রেস থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এই চিঠি গুলি ঔপন্যাসিক মুন্সি প্রেমচাঁদ হিন্দিতে অনুবাদ করেন, যার নাম 'পিতাকে পত্র পুত্রীকে নাম' এবং শোভন বসু-র অনুবাদ থেকে 'কল্যাণীয়াসু ইন্দু' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য চিঠিগুলির সংকলন হলো মূলত কন্যার প্রতি একজন স্নেহময় পিতার অমূল্য তত্ত্বাবধান ও উপদেশ।
● চিঠির বিষয়বস্তু : ইন্দিরাকে লেখা জওহরলাল নেহেরুর চিঠি গুলিতে পৃথিবীর উৎপত্তি তত্ত্ব থেকে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ বিষয়ে আলোচনা করা আছে। এই চিঠি গুলিতে জওহর পৃথিবীর উৎপত্তি, মানুষের আগমন, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, খাদ্যসংগ্রহ, আগুনের আবিষ্কার, কীভাবে রাজপদ সৃষ্টি হলো, কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের প্রচলন হলো, ভাষার উদ্ভব হলো, লিপির উদ্ভব, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, সমাজে শ্রেণী বিভাজনের কারণ প্রভৃতি নিয়ে সুন্দর ও সাবলীল আলোচনা করেছেন।
তিনি তাঁর চিঠিগুলিতে ধনীঘরে উদ্বৃত্ত ও গরিবদের খাদ্যসংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। দেশীয় রাজাদের বিলাসব্যসন ও শৌখিন গাড়ি চড়ার সমালোচনা করেছেন। প্রজাদের অন্নকষ্ট, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও শিক্ষার অভাবের কথা তুলে ধরেছেন। বিশ্ববাসীকে ভারতীয়দের আত্মীয় বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
চিঠিগুলিতে তিনি বিদেশি বস্ত্র না পরে 'খদ্দর' কিনে পরার মাধ্যমে দেশের গরিব তাঁতিদের সাহায্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি লেখেন যে, সুসজ্জিত পোশাক পরিহিত ও বন্দুক হাতে পাশ্চাত্যের লোক অপেক্ষা অর্ধনগ্ন ও নিরস্ত্র ভারতবাসী অধিক শক্তিশালী।
● চিঠিগুলির বৈশিষ্ট্য : এই চিঠি গুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, নিজের জাতি পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে গোটা মানবসমাজকে একই পরিবারের অঙ্গ হিসেবে চেনা এবং নিজের সন্তানকে এই উদার ভাবনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা।
● গুরুত্ব ও মূল্যায়ন : আলোচ্য চিঠিগুলিতে সমকালীন ঘটনা বা তার মূল্যায়নের কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে এই পত্রাবলির গুরুত্ব সামান্য। কিন্তু শিশুকন্যার ইতিহাস চেতনা গড়ে তোলার সূত্রে এই চিঠিগুলি থেকে রাজনীতিবিদ জওহরলালের বিশ্ব বিষয়ের বিশেষ পর্যালোচনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাসবোধ, রাষ্ট্রদর্শন, স্বদেশপ্রেম, নৈতিকতা, সমাজতন্ত্রে আগ্রহ, পরবর্তীকালে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণের ইঙ্গিত এসবই চিঠি গুলির মধ্যে নিহিত। ফলে স্বাধীন ভারতের রূপকার হিসেবে নেহরুর মূল্যায়ন করতে গেলে, তাঁর দর্শনের মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বুঝতে ও বিচার করতে হলে ইতিহাস গবেষকরা 'লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার' কে উপেক্ষা করতে পারেন না।
৯. আধুনিক ইতিহাস চর্চায় নারী ইতিহাসের গুরুত্ব আলোচনা করো।
■ নারী ইতিহাসচর্চা:
● ভূমিকা: ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে নারীসমাজের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক দেশের সমাজে নারীর স্থান মর্যাদাপূর্ণ হলেও অতীতে ভারতীয় সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত। অত্যাচার, নিপীড়ন, বধূ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হত নারীরা। পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে নারীর অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাবেক ইতিহাসে উপেক্ষিতা নারী সমাজের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন আধুনিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
● নারীবাদী ইতিহাসচর্চার গবেষণাঃ পাশ্চাত্যে নারীবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত হলেও ভারতের মতন দেশে এই চর্চা অপেক্ষাকৃত নবীন। ভারতে নারীবাদী ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন নীরা দেশাই, বি.আর.নন্দা, মালবিকা কার্লেকর প্রমুখ।
● নারী সমাজের ইতিহাসের গুরুত্ব : নারী ইতিহাস বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।
I. সমাজে নারীর অবস্থানঃ অতীতে উপেক্ষিতা নারী জাতি এখন গুরুত্ব সহকারে ইতিহাস চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, শিশুর উপর নিপীড়ন, বধূহত্যা, নারী নির্যাতন ও অন্যা অত্যাচার প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।
II. সমাজের অতীত রূপঃ লিঙ্গবৈষম্য, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক ব্যবস্থার কথা তুলে ধরে নারী ইতিহাস। ফলে এর থেকে আমরা সমাজের অতীত রূপ সম্পর্কে অবগত হই ।
III. অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠাঃ আলোচ্য ইতিহাসচর্চা নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতার উপর আলোকপাত করে, যা সমগ্র নারী সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস।
IV. সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠিঃ কোনো সমাজ বা সভ্যতায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদার উপর সেই সমাজের অগ্রসরতা বা পশ্চাদগামীতা নির্ভর করে। তাই নারী ইতিহাস হয়ে উঠেছে সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি।
● মন্তব্যঃ বর্তমান কালে নারী ইতিহাসচর্চা অনেকটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক ভারতীয় সমাজে নারীর সর্বব্যাপী অধিকার ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির যথার্থ মাপকাঠি। এই ভাবেই নারীদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতার পরিচয় নারী ইতিহাস চর্চায় স্থান লাভ করেছে।